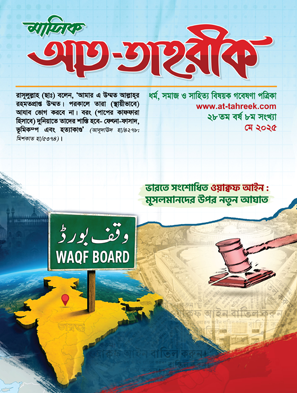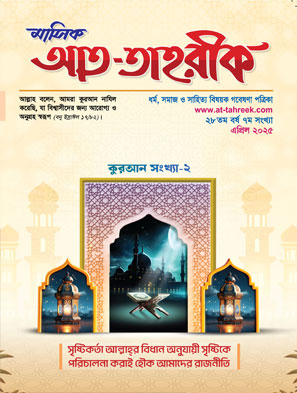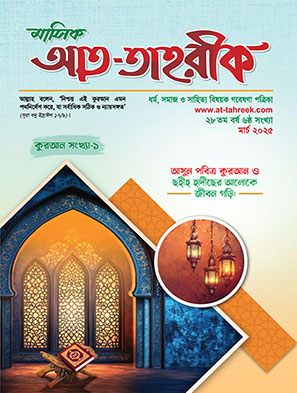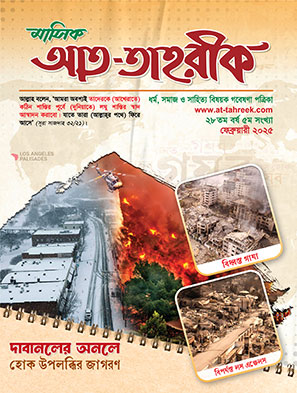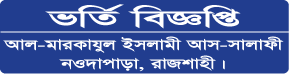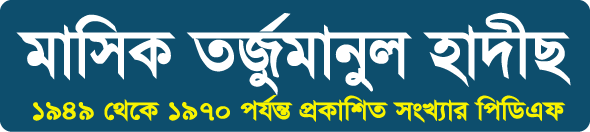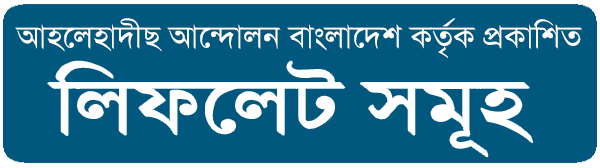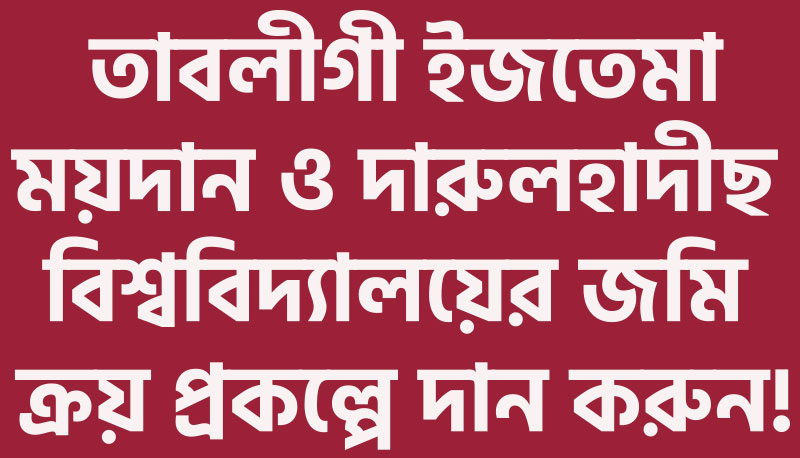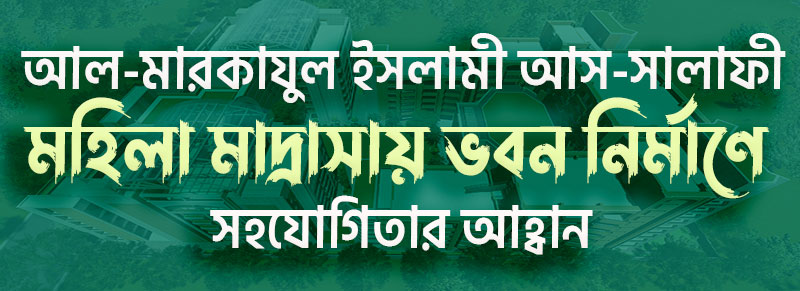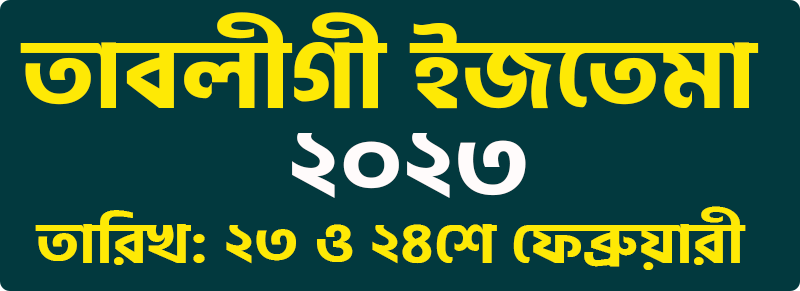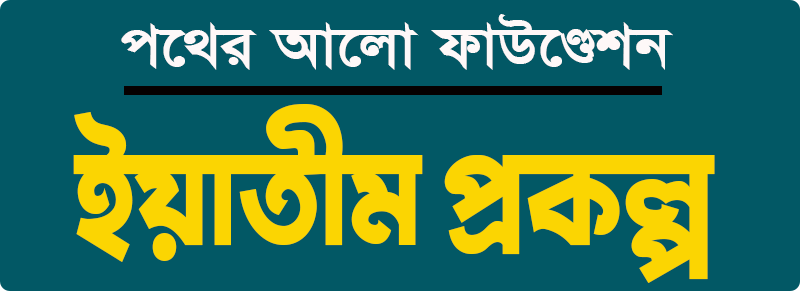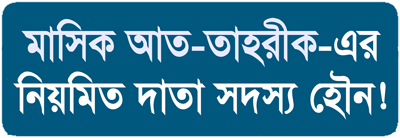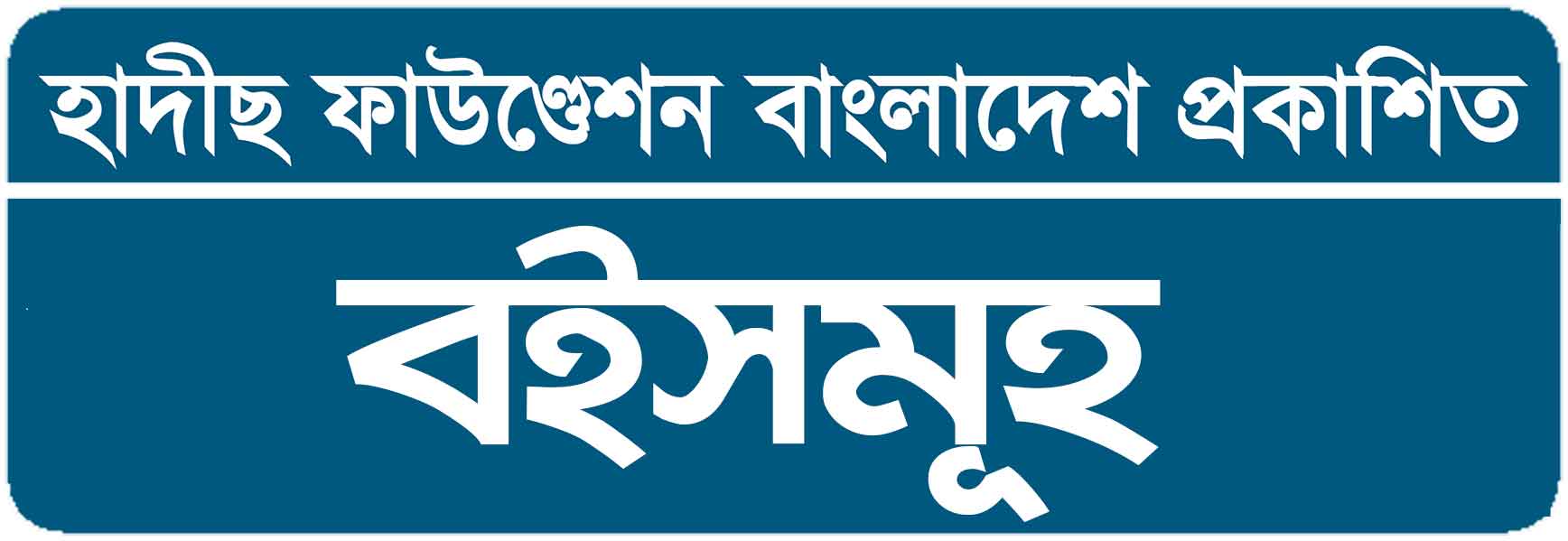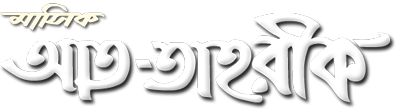

১. প্রখ্যাত তাবেঈ মুতাররিফ বিন শিখ্খীর (মৃ. ৯৫হি.) বলেন,ستّ خصال تعرف في الجاهل: الغضب في غير شيء، والكلام في غير نفع، والعطيّة في غير موضعها، وإفشاء السّر، والثقة بكلّ أحد، ولا يعرف صديقه من عدوه، ‘নির্বোধকে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চেনা যায় : (১) অকারণে রেগে যাওয়া, (২) অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, (৩) অপাত্রে দান করা, (৪) গোপনীয়তা ফাঁস করে দেওয়া, (৫) যে কাউকে বিশ্বাস করা, (৬) বন্ধুকে শত্রু থেকে আলাদা করতে না পারা’।[1]
২. ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেন,كنتُ آخذُ قدحًا مِن ماء زمزم، فأقرأُ عليه الفاتحة مرارًا، فأشربه؛ فأجدُ به من النفع، والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، ‘আমি একবার এক পেয়ালা যমযমের পানি নিলাম এবং সূরা ফাতিহা পড়ে তাতে কয়েকবার ফুঁক দিয়ে পান করলাম। ফলে আমি এর মাধ্যমে এমন উপকারিতা ও শক্তিমত্তা লাভ করলাম, যা কোন ঔষধেও কখনো পাইনি’।[2]
৩. ইমাম সারাখসী (মৃ. ৪৮৩হি.) বলেন, مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ الْبِدْعَةِ وَالسُّنَّةِ يَتْرُكُهُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْبِدْعَةِ لَازِمٌ وَأَدَاءُ السُّنَّةِ غَيْرُ لَازِمٍ، ‘কেউ যদি বিদ‘আত ও সুন্নাহর মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, তাহ’লে বিদ‘আতকে পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা বিদ‘আত পরিত্যাগ করা আবশ্যক আর সুন্নাত পালন করা আবশ্যক নয়’।[3]
৪. ইবনু রজব হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫হি.) বলেন, إذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه فاستحلى اللسان ذكر الله وما والاه وسرعت الجوارح إلى طاعة الله، ‘বান্দা যখন ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে এবং এর সুমিষ্টতা পেয়ে যায়, তখন তার জিহবা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এর প্রভাব ফুটে ওঠে। ফলে জিহবাতে আল্লাহর যিকর এবং তাঁর সন্তুষ্টিমূলক কথা মিষ্টি লাগে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর আনুগত্যের দিকে দ্রুত ধাবমান হয়’।[4]
৫. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) বলেন,بَعْضُ النَّاسِ يَحْتَجُّ لِتَرْكِ العلم بِكِبَرِ السِّنِّ، أَوْ عَدَمِ الذَّكَاءِ، أَوْ الْقِلَّةِ وَالْفَقْرِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَمِنْ ذَلِكَ وَسْوَاسُ الشَّيْطَانِ يُثَبِّطُونَ بِهَا، ‘ইলম অর্জন পরিত্যাগ করার জন্য কিছু মানুষ বয়স বেশী হওয়া, কম মেধা, সময়ের স্বল্পতা, দারিদ্র্য প্রভৃতির অজুহাত দেয়। অথচ এগুলো সবই শয়তানী কুমন্ত্রণা, যার কারণে তারা জ্ঞান অর্জনে হতোদ্যম হয়ে পড়ে’।[5]
৬. ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হি.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি ক্বিয়ামুল লায়ল আদায় না করে ঘুমায়, সে ক্বিয়ামুল লায়লের বদলে চাশতের ছালাত আদায় করে নিবে’।[6]
৭. ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮হি.) বলেন,العَدلُ نِظامُ كُلِّ شَيءٍ، فإذا أُقيمَ أمرُ الدُّنيا بعَدلٍ قامَت، وإنْ لم يكُنْ لصاحِبها في الآخِرةِ مِن خَلاقٍ، ومَتى لم تَقُمْ بعَدلٍ لم تَقُمْ، وإن كان لصاحِبها مِنَ الإيمانِ، ‘ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে সবকিছুর শৃঙ্খলা। অতএব দুনিয়ার কাজগুলো যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিচালিত হয়, তবে ইনছাফ প্রতিষ্ঠিত হবে, যদিও সেই ইনছাফকারী (কাফের হয়, যার) আখেরাতে কোন অংশ নেই। আর যখন (কোন কিছু) ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্পাদিত হয় না, তখন ইনছাফ প্রতিষ্ঠা পায় না, যদিও সেটা কোন ঈমানদার ব্যক্তি পরিচালনা করে’।[7]
৮. আবূ যাকারিয়া আল-আম্বারী (রহঃ) বলেন,عِلْمٌ بِلا أَدَبٍ كَنَارٍ بِلا حَطَبٍ وَأَدَبٌ بِلا عِلْمٍ كَرُوحٍ بِلا جِسْمٍ، ‘শিষ্টাচার বিহীন ইলম হচ্ছে কাঠবিহীন আগুনের মতো। আর ইলমবিহীন আদব হ’ল শরীর বিহীন আত্মার মতো’।[8]
৯. বছরার প্রখ্যাত খতীব শাবীব ইবনে শায়বাহ (মৃ. ১৭০ হি.) বলেন,من سمع كلمة يكرهها فسكت عنها انقطع عنه ما يكره، فإن أجاب عنها سمع أكثر مما يكره، ‘যে ব্যক্তি অপসন্দনীয় কোন কথা শোনার পর চুপ থাকে, তার খারাপ লাগাটা শীঘ্রই চলে যায়। কিন্তু সে যদি উত্তর দিতে যায়, তবে সে যা অপসন্দ করে তার চাইতে বেশী কিছু তাকে শুনতে হয়’।[9]
১০. ইবনুল জাওযী (৫০৮-৫৯৭ হি.) বলেন,ويتبين فهم الصبي وعلو همته وتقصيرها باختياراته لنفسه؛ وقد تجتمع الصبيان للعب فيقول العالي الهمة: من يكون معي، ويقول القاصر: مع من أكون. ومتى علت همته آثر العلم، ‘শিশুর বোধশক্তি, দৃঢ় হিম্মত বা তার কমতি বোঝা যায় নিজের জন্য সে কী বাছাই করে সেটা থেকে। শিশুরা যখন খেলাধুলা করতে জড়ো হয়, তখন উচ্চ মনোবলের অধিকারী ছেলেটা বলে, ‘আমার সাথে কে কে আসবে?’ আর যে ছেলের হিম্মত কম সে বলে, ‘আমি কার সাথে যাব?’ আর যে বাচ্চার হিম্মত অনেক বেশী হয়, সে ইলম অর্জনের পথ বাছাই করে নেয়’।[10]
আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ
এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় ও শিক্ষক,
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
[1]. ইবনু আব্দিল বার্র, বাহজাতুল মাজালিস, পৃ. ১১৭।
[2]. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ১/৫৮।
[3]. সারাখসী, আল-মাবসূত, ২/৮০।
[4]. ইবনু রজব, লাতাইফুল মা‘আরেফ, পৃ. ২২৬।
[5]. ইবনে মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারইয়াহ ১/২১৫।
[6]. ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া, ২২/২৮৪।
[7]. মাজমূ‘উল ফাতাওয়া, ২৮/১৪৬।
[8]. ইবনুল মুক্বাফফা‘, আল-আদাবুছ ছাগীর, পৃ. ১০।
[9]. ইবনু কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, উয়ূনুল আখবার ১/৪০০।
[10]. ইবনুল জাওযী, তাম্বীহুন নায়েম, পৃ. ৫২।
সর্বশেষ প্রবন্ধ
- মাসায়েলে কুরবানী
- যে আমলে সম্মান বাড়ে (পূর্ব প্রকাশিতের পর)
- সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে কুরআনে বর্ণিত শাস্তিবিধানের অপরিহার্যতা (শেষ কিস্তি)
- রিয়া-র আলামত
- কুরবানী কবুলযোগ্য করার উপায়
- নারী সংস্কার কমিশনের অন্যায় সুফারিশ সমূহ
- শাহ ইসমাঈল শহীদ : ভারতীয় উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালার
- যে আমলে সম্মান বাড়ে
- আল-কুরআনে নাসেখ ও মানসূখ (পূর্ব প্রকাশিতের পর)
- সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে কুরআনে বর্ণিত শাস্তিবিধানের অপরিহার্যতা (৩য় কিস্তি)
পুরাতন সংখ্যা
সর্বাধিক পঠিত প্রবন্ধ
- মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পরিণতি
- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবাসা
- তালাকের শারঈ পদ্ধতি ও হিল্লা বিয়ের বিধান
- ইসলামে দাড়ি রাখার বিধান
- হজ্জ : গুরুত্ব ও ফযীলত
- শিক্ষকের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিশুর পাঠদান পদ্ধতি ও শিখনফল নির্ণয়
- কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াতের ফযীলত
- আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য
- আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসা
- মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব (৩য় কিস্তি)